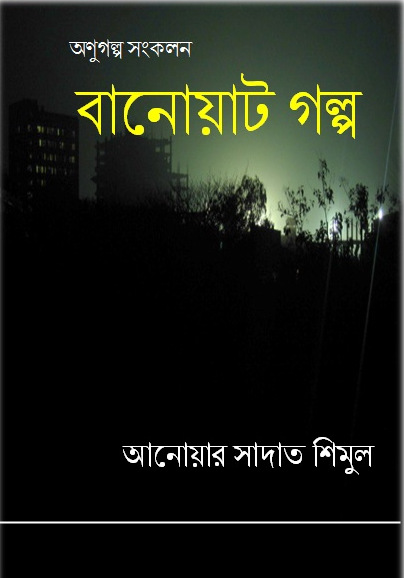লাইক অ্যা ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই
মানুষ কিলবিল করছে ঢাকা শহরে।
 কেবলই মানুষের ভীড়। দেশের নানান প্রান্ত থেকে আসা শীর্ণ বিশীর্ণ মানুষ, ছুটে চলা; শুধুই ক্লান্তি জাগায়। ট্রাফিক জ্যামে ঘিরে ধরে হাড্ডিসার জিরজিরে শরীর, এক চোখ নেই, দাঁত ভাঙা, হাত কাটা, পা কাটা, মুখের চামড়া ঝুলে পড়া, রোগাক্রান্ত শিশু – নারী – যুবা – বৃদ্ধ ভিক্ষুক। প্রতিদিন সেই একই দৃশ্য। এরচেয়ে বরং দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে ভালো লাগে, সাইনবোর্ডের বানানগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বানান ভুল বের করে সময় কাটে। ফেলে আসা দিন, ফেলে আসা সময়কে স্মৃতি করে রাখি, ভাবি – ওগুলো এরকমই এক সময়। সে সময়ের জন্য হা-হুতাশ করি না। তবুও মনে পড়ে টরন্টো ট্রানজিট কমিশনের ট্রেন। ‘সে রাতে পূর্ণিমা ছিল’ পড়তে পড়তে ইয়াং স্টেশনের বদলে কুইন্সে গিয়ে থামা। ভিক্টোরিয়া পার্ক স্টেশনে নরম রোদেলা দুপুরে রাইজ – ট্রাউটের ‘পজিশনিং ; ব্যাটেল ইন ইয়্যূর মাইন্ড’ পড়া। এখন এসব মনে পড়ে, যখন দেখি গুলশান এক নম্বর মোড়ে এক গাদা বই দুই হাতে চেপে এগিয়ে আসে হতদরিদ্র কিশোর হকার। সব ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস।
কেবলই মানুষের ভীড়। দেশের নানান প্রান্ত থেকে আসা শীর্ণ বিশীর্ণ মানুষ, ছুটে চলা; শুধুই ক্লান্তি জাগায়। ট্রাফিক জ্যামে ঘিরে ধরে হাড্ডিসার জিরজিরে শরীর, এক চোখ নেই, দাঁত ভাঙা, হাত কাটা, পা কাটা, মুখের চামড়া ঝুলে পড়া, রোগাক্রান্ত শিশু – নারী – যুবা – বৃদ্ধ ভিক্ষুক। প্রতিদিন সেই একই দৃশ্য। এরচেয়ে বরং দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে ভালো লাগে, সাইনবোর্ডের বানানগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বানান ভুল বের করে সময় কাটে। ফেলে আসা দিন, ফেলে আসা সময়কে স্মৃতি করে রাখি, ভাবি – ওগুলো এরকমই এক সময়। সে সময়ের জন্য হা-হুতাশ করি না। তবুও মনে পড়ে টরন্টো ট্রানজিট কমিশনের ট্রেন। ‘সে রাতে পূর্ণিমা ছিল’ পড়তে পড়তে ইয়াং স্টেশনের বদলে কুইন্সে গিয়ে থামা। ভিক্টোরিয়া পার্ক স্টেশনে নরম রোদেলা দুপুরে রাইজ – ট্রাউটের ‘পজিশনিং ; ব্যাটেল ইন ইয়্যূর মাইন্ড’ পড়া। এখন এসব মনে পড়ে, যখন দেখি গুলশান এক নম্বর মোড়ে এক গাদা বই দুই হাতে চেপে এগিয়ে আসে হতদরিদ্র কিশোর হকার। সব ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস।
দাম জিজ্ঞেস করতেই মনে হলো, এদের টার্গেট গ্রুপ ভিন্ন। আমি হাসি, বলি – পড়ার জন্য বই কিনি, ঘর সাজানোর জন্য না। তারপর দরাদরি শেষে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মোড়ক খুলে উপন্যাসের পাতা উল্টাই – ‘লাইক অ্যা ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই’, লিখেছেন সাজিয়া ওমর।
গরমাগরম রিভিউ, আলাপ, প্রশংসা সব হয়ে হয়ে গেছে আগে। ডেইলি স্টারে বই নিয়ে আলাপ দেখেছি, অন্য একাধিক বাংলা দৈনিকের নারী পাতায় লেখকের ছবি -সাক্ষাতকার দেখেছি, চোখ বুলিয়েছি। বলা হয়েছে, এ সময়কার ঢাকা শহর, মাদকাসক্ত তারুণ্য, দারিদ্র্য; এসবই উপজীব্য। বইয়ের প্রথম দু’তিন পাতা যখন পড়লাম, টের পেলাম লেখায় গতি আছে বেশ। গল্পের প্রধান দুটো চরিত্র দ্বীন (Deen) এবং এজে (AJ) যখন কামাল আতাতুর্ক এভিনিউর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে পৌঁছে, তখন আরো মনোযোগী হই, বছর ছয়েক আগে ফেলে আসা এই আমাকে খুঁজি সাজিয়া ওমরের জনকোলাহলে। হতাশ হতে হলো শুরুতেই, যে আম গাছের নিচে গিয়ে দ্বীন বসে, যে লবিতে মারিয়া হেঁটে আসে, যে ক্যান্টিন বর্ণনা পায়; সেসব আমার অদেখা। এরপর এই ভেবে পাতা উল্টাই যে এটা ডকু ফিকশন নয়, নিছক ফিকশন। আমার শেষ-কৈশোরের ক্যাম্পাসের ধুলো এসব পাতায় না থাকলে ক্ষতি নেই। কিছু বিরতি ছিল পাঠে, ক্লান্তি লাগেনি, চল্লিশ-পঞ্চাশ পৃষ্ঠা শেষ হয়ে গেলে মোট পৃষ্ঠা গুনে দেখি দু’শ বায়ান্ন।
ঢাকার উঠতি অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির সামাজিক শৈথিল্য, বিচ্ছিন্নতা, ভুল তরুণ দল আর প্রেম অপ্রেমের জীবন ছোঁয়ায় সাজিয়া ওমর সফল হয়েছেন, ঠিক। তবে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন ঠিক কোন জায়গায় গিয়ে থামতে হবে, কোন জায়গায় পাঠককে অপেক্ষা করাতে হবে; এসব নির্ধারণে। দ্বীন এবং এজে দুটো প্যারালাল চরিত্র। টঙ্গীর বস্তিতে ফালানির ঘরে এরা ধোঁয়ায় মগ্ন হয়। এদের অসম বন্ধুরা, সাগর – রাহুল – পারভেজ – মুসা – কালা এবং অনেকে, সঙ্গে থাকে। নিজেরা স্বীকার করে এরা খোর, khor2core। ওরা স্বীকার করে সুস্থ জীবনে আর ফেরা যাবে না। তাই ওরা ছোটে আর ছোটে। তাদের নিজস্ব গল্প আছে, ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা আর গ্লানি আছে। দ্বীন যেমন তার বাবার মৃত্যুর জন্য নিজেকে অপরাধী করে, এজে যেমন রাজ গোপালের অপরাধ নেটওয়ার্কে জড়িয়ে পরিবারকে অর্থ ঋণভার থেকে বাঁচায়, তেমন করে বাস্তবতা হয়ে ওঠে অস্থির জীবনের যাত্রা। তাই তারা আশ্রয় খোঁজে।
এজে আশ্রয় খোঁজে রাজ গোপালের কেপ্ট ভারতীয় সুন্দরীর কাছে। দ্বীন আশ্রয় খোঁজে মারিয়ার কাছে। ব্রোকেন ফ্যামিলির মেয়ে মারিয়া, যাকে এজে ম্যান-ইটার বলে। তবুও দ্বীন মারিয়ার জন্য অপেক্ষা করে। তবে এসব অপেক্ষা-আশ্রয় প্লেটোনিক নয়। রয়েছে, প্রবল শরীরি আকর্ষণ। সুন্দরী-মারিয়া দুজনই নিজেদের মেলে ধরে। বাঙালি লেখকের কলমে সেক্স বিত্তান্তে রূপক থাকে প্রায়শ, এখানে সাজিয়া ওমর ট্রেন্ড ভাঙতে পেরেছেন কিনা সে আলাপ অন্য সময়ে করা যাবে, তবে সাজিয়া সাবলীল ছিলেন বিবরণে। এ বিবরণ আবার নতুন কিছু নয়। অনেক ক্ষেত্রে শিডনী শেলডনের তুমুল প্রভাব কিংবা ছায়া এসেছে সেসব বিবরণে। এক সময় এসে মনে হয়েছে, বড়ো বেশি শরীরি গল্পের কাহিনী হয়ে যাচ্ছে এ উপন্যাস, সেক্স অ্যান্ড সিটির কাহিনী এগুচ্ছে না। মাদকাসক্ত – বিষন্ন মানুষ এমন করে ফ্রয়েড আক্রান্ত হয় কিনা সে প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তিগত জীবনে সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট সাজিয়া ওমরই ভালো বলতে পারবেন।
গল্পের কাঠামো সাজানোয় কৌশলের কথা বলছিলাম। উপন্যাসটি সরল রৈখিক নয়। দ্বীন, এজে, মারিয়া, ফালানি, সুন্দরী, রাজ গোপাল, পারভেজ, চিঙ্কস, সার্জেন্ট আকবর; এদের সবাই যখন পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত হয় – তখন অনেকগুলো গল্পের ভেতরে গল্পের সম্ভবনা জেগে ওঠে। হয়তো পৃষ্ঠা সীমিত ছিল, নইলে লেখক অমনোযোগী অথবা নিতান্তই অবহেলায় এরকম অনেক সম্ভাব্য গল্পের প্লটকে খুন করা হয়েছে।
পারভেজের মৃত্যু এবং এর বিবরণ দূর্দান্ত। মাদকাসক্ত চিঙ্কসের (চিঙ্কু) মৃত্যুতে বাস্তবতা ছিল, করুণ বেদনা ছিল, ভয় ছিল। কিন্তু, পারভেজের মৃত্যু যেন পরাবাস্তবতা। পারভেজের বাবা যিনি মন্ত্রী মিন্টু চাচা নামে উপন্যাসে আগেও এসেছেন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলে এজে-দ্বীনদের চারপাশে সব কিছু ভেঙে পড়ে। এই মন্ত্রীকে খুব চেনা চেনা লাগে, যেমন চেনা লাগে রাজ গোপালকে। সাজিয়া ওমর অবশ্য রাজ গোপালকে আরো আড়াল দিতে পারতেন চাইলে, অন্ততঃ সেটাই ভালো হতো। ফিকশনকে ফিকশন রাখা ভালো। পারভেজের বাসায় পার্টিতে অর্থমন্ত্রীর ছেলে কিংবা কৃষি মন্ত্রীর তিনকন্যা; এদের না চিনলেও চলে। কিন্তু রাজ গোপাল, হয়তো আমাদের মিডিয়া গসিপের কারণেই, চেনা হয়ে যায়। সার্জেন্ট আকবর আরেকটি দারুণ চরিত্র। কামকাতুর-ধর্মভীরু মধ্যবিত্ত লোক, যে কিনা শুধু মেয়ের টিউশনের জন্য ঘুষ খায়। ভেতরে ভেতরে হিরো হওয়ার স্বপ্ন দেখে, খুশি হয়ে সবজি সমুচার বদলে গরু মাংসের সমুচা খায়। আকবরকে নিয়ে কম বেশি করা হয়নি। তবে অযত্ন ছিল, ফালানি এবং সুন্দরীকে নিয়ে। এ দুটো সম্ভবনাময় চরিত্র অবহেলায় থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত।
উপন্যাসের অন্তত দুটো জায়গায় র্যা বকে ফোর্সেস উইথ লাইসেন্স টু কিল বলা হয়েছে। Government of Bangladesh কে GOB ডেকে বিষেদাগার করা হয়েছে। হয়তো রটেন অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি এসব বলেই সান্ত্বনা পায়। জীবন জীবিকার সংগ্রাম যেখানে অনুপস্থিত, পড়ালেখাও যখন স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে ওঠে তখন দ্বীনের যৌক্তিক ব্যাখ্যাকে অহেতুক লাগে – “He didn’t want to be part of this system. BBA, MBA, fast track to the grand life where you spend your precious hours like a greedy bastard salivating over balance sheets for some foreign firm that rips resources off your land and degrade your people to poverty.” শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু যখন কে এই কথাটা বললো সেটা সামনে আসে – তখন দ্বীনের এই দার্শনিকতা ভন্ডামি হয়ে যায়।
ব্যক্তিগত শুন্যতায় মারিয়া বলে, “I feel so alone,”…”Disconnected. And it’s not just my life I hate. Everyone seems pathetic. No one is happy. No one’s found deeper bliss or any reason for living. People like to dwell in their shitty little lives out of habit. Even you, Deen, your life is a waste of time.”
যদিও এই ঋণাত্বক ভাবনা বিলাসীতা নয়, কিন্তু এই যদি হয় জীবনবোধ, এই যদি হয় জীবনাচরণ – তখন ওয়েটিং ফর গডো ছাড়া আর উপায় নেই। গডো আসে না, আসে মৃত্যু। ক্ষমতা ও সম্পর্কের সমস্ত আশ্রয় তখন ভেঙে পড়ে।
ফিকশন তো ফিকশনই থাকবে। কোথায় যেন পড়েছিলাম - Fiction is not reality but fiction should reflect reality and reality is that what exists in our life. পড়তে গিয়ে অনেকবার মনে হয়েছে, বড্ডো বেশি কল্পনা হয়ে যাচ্ছে, এ আমাদের শহর নয়, এ আমাদের মানুষ নয়। এসব অন্য শহরের কাহিনী। শেষের দিকে পারভেজ যখন চিৎকার করে, “everything happens in Bangladesh, behind closed doors” তখন দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছু থাকে না। দরজার ওপাশে সাজিয়া ওমর গিয়েছেন, দেখেছেন-শুনেছেন-বলেছেন। তাই অভিনন্দন।
ডেব্যু ইনিংস বলে কিছু ভুল শটের চেষ্টাগুলো ক্ষমা করে দেয়া যায়। সাজিয়া ওমরের পরবর্তী বইটি পড়ার অপেক্ষায় রইলাম।
‘লাইক অ্যা ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই’ শেষ করার পরে এক ধরণের মন খারাপ চেপে বসেছে। শেষ আট পৃষ্ঠা, সমাপ্তি, আমাকে বিষন্ন করেছে। দ্বীনের জন্য সমবেদনা নাকি করুণা থাকবে সেটি বলতে পারছি না। তবে দ্বীনের সংখ্যা বাড়ছে, অসংখ্যা এজে মোটরবাইকে ছুটছে, মারিয়ারা আরো বিভ্রান্ত হচ্ছে, পারভেজ ডুবে যাচ্ছে মেঘনা নদীতে, নতুন কোনো রাজ গোপাল আরো শীতল হাসি হাসছে। আশুলিয়ার জলে ভেসে যাওয়া জোছনা নয়, আমাদের শহরের নিয়ন আলো ম্লান করে ডিজে নাইটের শীৎকারে ধোঁয়া বাড়ে, স্বপ্নরা হারিয়ে যায় আকাশে। লাইক অ্যা ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই।
.
.
.
Read more...
 কেবলই মানুষের ভীড়। দেশের নানান প্রান্ত থেকে আসা শীর্ণ বিশীর্ণ মানুষ, ছুটে চলা; শুধুই ক্লান্তি জাগায়। ট্রাফিক জ্যামে ঘিরে ধরে হাড্ডিসার জিরজিরে শরীর, এক চোখ নেই, দাঁত ভাঙা, হাত কাটা, পা কাটা, মুখের চামড়া ঝুলে পড়া, রোগাক্রান্ত শিশু – নারী – যুবা – বৃদ্ধ ভিক্ষুক। প্রতিদিন সেই একই দৃশ্য। এরচেয়ে বরং দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে ভালো লাগে, সাইনবোর্ডের বানানগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বানান ভুল বের করে সময় কাটে। ফেলে আসা দিন, ফেলে আসা সময়কে স্মৃতি করে রাখি, ভাবি – ওগুলো এরকমই এক সময়। সে সময়ের জন্য হা-হুতাশ করি না। তবুও মনে পড়ে টরন্টো ট্রানজিট কমিশনের ট্রেন। ‘সে রাতে পূর্ণিমা ছিল’ পড়তে পড়তে ইয়াং স্টেশনের বদলে কুইন্সে গিয়ে থামা। ভিক্টোরিয়া পার্ক স্টেশনে নরম রোদেলা দুপুরে রাইজ – ট্রাউটের ‘পজিশনিং ; ব্যাটেল ইন ইয়্যূর মাইন্ড’ পড়া। এখন এসব মনে পড়ে, যখন দেখি গুলশান এক নম্বর মোড়ে এক গাদা বই দুই হাতে চেপে এগিয়ে আসে হতদরিদ্র কিশোর হকার। সব ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস।
কেবলই মানুষের ভীড়। দেশের নানান প্রান্ত থেকে আসা শীর্ণ বিশীর্ণ মানুষ, ছুটে চলা; শুধুই ক্লান্তি জাগায়। ট্রাফিক জ্যামে ঘিরে ধরে হাড্ডিসার জিরজিরে শরীর, এক চোখ নেই, দাঁত ভাঙা, হাত কাটা, পা কাটা, মুখের চামড়া ঝুলে পড়া, রোগাক্রান্ত শিশু – নারী – যুবা – বৃদ্ধ ভিক্ষুক। প্রতিদিন সেই একই দৃশ্য। এরচেয়ে বরং দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে ভালো লাগে, সাইনবোর্ডের বানানগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বানান ভুল বের করে সময় কাটে। ফেলে আসা দিন, ফেলে আসা সময়কে স্মৃতি করে রাখি, ভাবি – ওগুলো এরকমই এক সময়। সে সময়ের জন্য হা-হুতাশ করি না। তবুও মনে পড়ে টরন্টো ট্রানজিট কমিশনের ট্রেন। ‘সে রাতে পূর্ণিমা ছিল’ পড়তে পড়তে ইয়াং স্টেশনের বদলে কুইন্সে গিয়ে থামা। ভিক্টোরিয়া পার্ক স্টেশনে নরম রোদেলা দুপুরে রাইজ – ট্রাউটের ‘পজিশনিং ; ব্যাটেল ইন ইয়্যূর মাইন্ড’ পড়া। এখন এসব মনে পড়ে, যখন দেখি গুলশান এক নম্বর মোড়ে এক গাদা বই দুই হাতে চেপে এগিয়ে আসে হতদরিদ্র কিশোর হকার। সব ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস। দাম জিজ্ঞেস করতেই মনে হলো, এদের টার্গেট গ্রুপ ভিন্ন। আমি হাসি, বলি – পড়ার জন্য বই কিনি, ঘর সাজানোর জন্য না। তারপর দরাদরি শেষে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মোড়ক খুলে উপন্যাসের পাতা উল্টাই – ‘লাইক অ্যা ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই’, লিখেছেন সাজিয়া ওমর।
গরমাগরম রিভিউ, আলাপ, প্রশংসা সব হয়ে হয়ে গেছে আগে। ডেইলি স্টারে বই নিয়ে আলাপ দেখেছি, অন্য একাধিক বাংলা দৈনিকের নারী পাতায় লেখকের ছবি -সাক্ষাতকার দেখেছি, চোখ বুলিয়েছি। বলা হয়েছে, এ সময়কার ঢাকা শহর, মাদকাসক্ত তারুণ্য, দারিদ্র্য; এসবই উপজীব্য। বইয়ের প্রথম দু’তিন পাতা যখন পড়লাম, টের পেলাম লেখায় গতি আছে বেশ। গল্পের প্রধান দুটো চরিত্র দ্বীন (Deen) এবং এজে (AJ) যখন কামাল আতাতুর্ক এভিনিউর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে পৌঁছে, তখন আরো মনোযোগী হই, বছর ছয়েক আগে ফেলে আসা এই আমাকে খুঁজি সাজিয়া ওমরের জনকোলাহলে। হতাশ হতে হলো শুরুতেই, যে আম গাছের নিচে গিয়ে দ্বীন বসে, যে লবিতে মারিয়া হেঁটে আসে, যে ক্যান্টিন বর্ণনা পায়; সেসব আমার অদেখা। এরপর এই ভেবে পাতা উল্টাই যে এটা ডকু ফিকশন নয়, নিছক ফিকশন। আমার শেষ-কৈশোরের ক্যাম্পাসের ধুলো এসব পাতায় না থাকলে ক্ষতি নেই। কিছু বিরতি ছিল পাঠে, ক্লান্তি লাগেনি, চল্লিশ-পঞ্চাশ পৃষ্ঠা শেষ হয়ে গেলে মোট পৃষ্ঠা গুনে দেখি দু’শ বায়ান্ন।
ঢাকার উঠতি অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির সামাজিক শৈথিল্য, বিচ্ছিন্নতা, ভুল তরুণ দল আর প্রেম অপ্রেমের জীবন ছোঁয়ায় সাজিয়া ওমর সফল হয়েছেন, ঠিক। তবে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন ঠিক কোন জায়গায় গিয়ে থামতে হবে, কোন জায়গায় পাঠককে অপেক্ষা করাতে হবে; এসব নির্ধারণে। দ্বীন এবং এজে দুটো প্যারালাল চরিত্র। টঙ্গীর বস্তিতে ফালানির ঘরে এরা ধোঁয়ায় মগ্ন হয়। এদের অসম বন্ধুরা, সাগর – রাহুল – পারভেজ – মুসা – কালা এবং অনেকে, সঙ্গে থাকে। নিজেরা স্বীকার করে এরা খোর, khor2core। ওরা স্বীকার করে সুস্থ জীবনে আর ফেরা যাবে না। তাই ওরা ছোটে আর ছোটে। তাদের নিজস্ব গল্প আছে, ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা আর গ্লানি আছে। দ্বীন যেমন তার বাবার মৃত্যুর জন্য নিজেকে অপরাধী করে, এজে যেমন রাজ গোপালের অপরাধ নেটওয়ার্কে জড়িয়ে পরিবারকে অর্থ ঋণভার থেকে বাঁচায়, তেমন করে বাস্তবতা হয়ে ওঠে অস্থির জীবনের যাত্রা। তাই তারা আশ্রয় খোঁজে।
এজে আশ্রয় খোঁজে রাজ গোপালের কেপ্ট ভারতীয় সুন্দরীর কাছে। দ্বীন আশ্রয় খোঁজে মারিয়ার কাছে। ব্রোকেন ফ্যামিলির মেয়ে মারিয়া, যাকে এজে ম্যান-ইটার বলে। তবুও দ্বীন মারিয়ার জন্য অপেক্ষা করে। তবে এসব অপেক্ষা-আশ্রয় প্লেটোনিক নয়। রয়েছে, প্রবল শরীরি আকর্ষণ। সুন্দরী-মারিয়া দুজনই নিজেদের মেলে ধরে। বাঙালি লেখকের কলমে সেক্স বিত্তান্তে রূপক থাকে প্রায়শ, এখানে সাজিয়া ওমর ট্রেন্ড ভাঙতে পেরেছেন কিনা সে আলাপ অন্য সময়ে করা যাবে, তবে সাজিয়া সাবলীল ছিলেন বিবরণে। এ বিবরণ আবার নতুন কিছু নয়। অনেক ক্ষেত্রে শিডনী শেলডনের তুমুল প্রভাব কিংবা ছায়া এসেছে সেসব বিবরণে। এক সময় এসে মনে হয়েছে, বড়ো বেশি শরীরি গল্পের কাহিনী হয়ে যাচ্ছে এ উপন্যাস, সেক্স অ্যান্ড সিটির কাহিনী এগুচ্ছে না। মাদকাসক্ত – বিষন্ন মানুষ এমন করে ফ্রয়েড আক্রান্ত হয় কিনা সে প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তিগত জীবনে সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট সাজিয়া ওমরই ভালো বলতে পারবেন।
গল্পের কাঠামো সাজানোয় কৌশলের কথা বলছিলাম। উপন্যাসটি সরল রৈখিক নয়। দ্বীন, এজে, মারিয়া, ফালানি, সুন্দরী, রাজ গোপাল, পারভেজ, চিঙ্কস, সার্জেন্ট আকবর; এদের সবাই যখন পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত হয় – তখন অনেকগুলো গল্পের ভেতরে গল্পের সম্ভবনা জেগে ওঠে। হয়তো পৃষ্ঠা সীমিত ছিল, নইলে লেখক অমনোযোগী অথবা নিতান্তই অবহেলায় এরকম অনেক সম্ভাব্য গল্পের প্লটকে খুন করা হয়েছে।
পারভেজের মৃত্যু এবং এর বিবরণ দূর্দান্ত। মাদকাসক্ত চিঙ্কসের (চিঙ্কু) মৃত্যুতে বাস্তবতা ছিল, করুণ বেদনা ছিল, ভয় ছিল। কিন্তু, পারভেজের মৃত্যু যেন পরাবাস্তবতা। পারভেজের বাবা যিনি মন্ত্রী মিন্টু চাচা নামে উপন্যাসে আগেও এসেছেন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলে এজে-দ্বীনদের চারপাশে সব কিছু ভেঙে পড়ে। এই মন্ত্রীকে খুব চেনা চেনা লাগে, যেমন চেনা লাগে রাজ গোপালকে। সাজিয়া ওমর অবশ্য রাজ গোপালকে আরো আড়াল দিতে পারতেন চাইলে, অন্ততঃ সেটাই ভালো হতো। ফিকশনকে ফিকশন রাখা ভালো। পারভেজের বাসায় পার্টিতে অর্থমন্ত্রীর ছেলে কিংবা কৃষি মন্ত্রীর তিনকন্যা; এদের না চিনলেও চলে। কিন্তু রাজ গোপাল, হয়তো আমাদের মিডিয়া গসিপের কারণেই, চেনা হয়ে যায়। সার্জেন্ট আকবর আরেকটি দারুণ চরিত্র। কামকাতুর-ধর্মভীরু মধ্যবিত্ত লোক, যে কিনা শুধু মেয়ের টিউশনের জন্য ঘুষ খায়। ভেতরে ভেতরে হিরো হওয়ার স্বপ্ন দেখে, খুশি হয়ে সবজি সমুচার বদলে গরু মাংসের সমুচা খায়। আকবরকে নিয়ে কম বেশি করা হয়নি। তবে অযত্ন ছিল, ফালানি এবং সুন্দরীকে নিয়ে। এ দুটো সম্ভবনাময় চরিত্র অবহেলায় থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত।
উপন্যাসের অন্তত দুটো জায়গায় র্যা বকে ফোর্সেস উইথ লাইসেন্স টু কিল বলা হয়েছে। Government of Bangladesh কে GOB ডেকে বিষেদাগার করা হয়েছে। হয়তো রটেন অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি এসব বলেই সান্ত্বনা পায়। জীবন জীবিকার সংগ্রাম যেখানে অনুপস্থিত, পড়ালেখাও যখন স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে ওঠে তখন দ্বীনের যৌক্তিক ব্যাখ্যাকে অহেতুক লাগে – “He didn’t want to be part of this system. BBA, MBA, fast track to the grand life where you spend your precious hours like a greedy bastard salivating over balance sheets for some foreign firm that rips resources off your land and degrade your people to poverty.” শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু যখন কে এই কথাটা বললো সেটা সামনে আসে – তখন দ্বীনের এই দার্শনিকতা ভন্ডামি হয়ে যায়।
ব্যক্তিগত শুন্যতায় মারিয়া বলে, “I feel so alone,”…”Disconnected. And it’s not just my life I hate. Everyone seems pathetic. No one is happy. No one’s found deeper bliss or any reason for living. People like to dwell in their shitty little lives out of habit. Even you, Deen, your life is a waste of time.”
যদিও এই ঋণাত্বক ভাবনা বিলাসীতা নয়, কিন্তু এই যদি হয় জীবনবোধ, এই যদি হয় জীবনাচরণ – তখন ওয়েটিং ফর গডো ছাড়া আর উপায় নেই। গডো আসে না, আসে মৃত্যু। ক্ষমতা ও সম্পর্কের সমস্ত আশ্রয় তখন ভেঙে পড়ে।
ফিকশন তো ফিকশনই থাকবে। কোথায় যেন পড়েছিলাম - Fiction is not reality but fiction should reflect reality and reality is that what exists in our life. পড়তে গিয়ে অনেকবার মনে হয়েছে, বড্ডো বেশি কল্পনা হয়ে যাচ্ছে, এ আমাদের শহর নয়, এ আমাদের মানুষ নয়। এসব অন্য শহরের কাহিনী। শেষের দিকে পারভেজ যখন চিৎকার করে, “everything happens in Bangladesh, behind closed doors” তখন দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছু থাকে না। দরজার ওপাশে সাজিয়া ওমর গিয়েছেন, দেখেছেন-শুনেছেন-বলেছেন। তাই অভিনন্দন।
ডেব্যু ইনিংস বলে কিছু ভুল শটের চেষ্টাগুলো ক্ষমা করে দেয়া যায়। সাজিয়া ওমরের পরবর্তী বইটি পড়ার অপেক্ষায় রইলাম।
‘লাইক অ্যা ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই’ শেষ করার পরে এক ধরণের মন খারাপ চেপে বসেছে। শেষ আট পৃষ্ঠা, সমাপ্তি, আমাকে বিষন্ন করেছে। দ্বীনের জন্য সমবেদনা নাকি করুণা থাকবে সেটি বলতে পারছি না। তবে দ্বীনের সংখ্যা বাড়ছে, অসংখ্যা এজে মোটরবাইকে ছুটছে, মারিয়ারা আরো বিভ্রান্ত হচ্ছে, পারভেজ ডুবে যাচ্ছে মেঘনা নদীতে, নতুন কোনো রাজ গোপাল আরো শীতল হাসি হাসছে। আশুলিয়ার জলে ভেসে যাওয়া জোছনা নয়, আমাদের শহরের নিয়ন আলো ম্লান করে ডিজে নাইটের শীৎকারে ধোঁয়া বাড়ে, স্বপ্নরা হারিয়ে যায় আকাশে। লাইক অ্যা ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই।
.
.
.