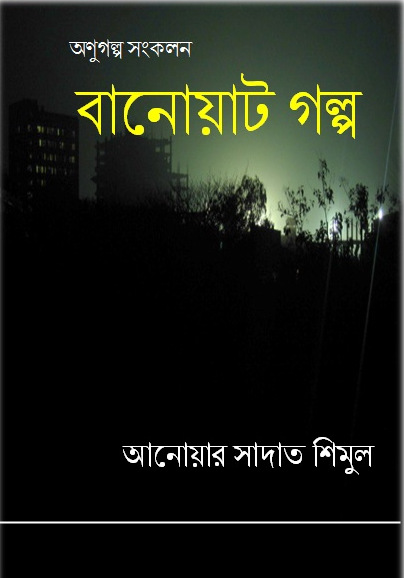ওকে, কাট
মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর সিনেমা ‘থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার’ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হয়েছে ব্যাপক। ইন্টারনেটে, সামাজিক মহলে আলাপ আলোচনায় তিন ধরনের মন্তব্য খেয়াল করেছি - ১) ফারুকীর পর্ণ ম্যুভি ২) ফাটাফাটি, জোস ৩) কনসেপ্ট ভাল, তবে আহামারী কিছু না।
দেখার ইচ্ছা থাকলেও নানান ঝুট ঝামেলা আর সুযোগের অভাবে সিনেমাটি দেখিনি। রিলিজের প্রায় বছর খানেক পরে, কিছুটা অবসর মিললে, গত সপ্তাহে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ডিভিডি কিনলাম। দেখলাম। নিজস্ব মতামতে ওপরের তিন নাম্বারে নিজেকে রাখবো। সব মানুষই একা, নোবডি বিলংস টু নোওয়ান; এটা যদি মূল বক্তব্য হয়, তবে তার পরিবেশনা ভীষণ দূর্বল ছিল। এরকম কনসেপ্টের ছবি বিশ্বে নতুন নয়, তাই চমকের কিছু নেই। কিন্তু, প্রচার প্রসারে যেটা ঢোল বাজিয়ে বলা হচ্ছিলো একাকী মেয়ের জীবন-দ্বিধা-সংকট, সেসবের ছায়া হয়তো আছে সিনেমাটিতে কিন্তু দর্শককে আক্রান্ত করার মতো না। অন্তত আমি আক্রান্ত হইনি। তিশার একঘেঁয়ে অভিনয় দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে ছিলাম আগে, এখানেও তা-ই হলো। মূল সমস্যা মনে হয়েছে – ফারুকী একসাথে অনেক কিছু দেখাতে চেয়েছে – তাই ফোকাস সরে গেছে বারবার। একাকী মেয়ের জীবন, প্রেম-অপ্রেমের সম্পর্ক, নাকি পারস্পরিক দ্বিধা; সব মিলিয়ে খাপছাড়া লেগেছে সব। খুব কাছের এক মানুষ, ব্যক্তিগত জীবনে বাঙালি-সামাজিকতা-সংরক্ষণশীলতার পক্ষে তিনি, সিনেমা দেখে আমাকে বলেছিলেন – “আমাদের সামনের সীটে বাবা আর মেয়ে বসেছিল, ছিঃ ছিঃ কী বিব্রত অবস্থা!”
এবার সিনেমা দেখতে দেখতে বিব্রত অবস্থা নিয়ে ভাবলাম, হ্যাঁ ঠিক – মনে হয়েছে আমাদের ‘সামাজিক’ প্রেক্ষিতে ‘এখনো’ বাবা মেয়ে বসে এ সিনেমা দেখাটা কিছুটা অস্বস্তির। পালটা প্রশ্ন যেমন আসে, মল্লিকা শেরওয়াত যখন খুল্লামখুল্লা নাচে মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমের বক্সে তখন ফারুকীর সিনেমায় দোষ কোথায়? ওরকম যৌন আবেদন তো নেই। আবেদন নেই, সত্যি। কিন্তু ইংগিত আছে ব্যাপক। বয়স্ক লোলুপ কচি খন্দকার বারবার ‘আই ওয়ান্না ফাক ইউ’ গান শোনালে তিশা জিজ্ঞেস করে ‘শুধু গান শুননেই আপনার হয়ে যায়?” কাশবনের ভেতরে তপু যখন তিশাকে আড়াল থেকে আড়ালে নিয়ে যায় তখন তিশা ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করে ‘আজ সতীত্ব নিয়ে ফিরতে পারবো তো?’ এর পরে আছে ‘ঋণ শোধ’এর জন্য শারীরিক সম্পর্কের ডাক। তপু ফার্মাসীর সামনে নিরোধক কেনার জন্য ঘুর ঘুর করছে, একবার স্যালাইন কিনে, পরেরবার সফল হয়। মাঝে আছে মধ্যরাতে এক ফ্ল্যাটে তপু-তিশার জেগে থাকা, সেখানেও শরীরি ডাক প্রবল। এসব দৃশ্য ইংগিত সংলাপ বেশিরভাগ দর্শকের কাছে অস্বস্তিকর লাগতেই পারে। সুতরাং, আপত্তির জায়গাটা একেবারে ফেলে দেয়ার নয়।
থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারকে আমি রেটিং দেবো পাঁচে তিন।
তবে ছবির গানগুলো শুনছি প্রায় বছর দেড়েক ধরে। সেগুলোকে চার।
ছবি শেষ হওয়ার পরে, ডিভিডির স্পেশাল ফিচার-এ ক্লিক করলাম। সিনেমা বানানোর পেছনের দৃশ্য, মুছে দেয়া দৃশ্য, কুশীলবদের সাক্ষাতকার, বিজ্ঞাপন, পোস্টার, ফটো এলবাম এসবের সঙ্গে আছে ফারুকীর করা ১৩ মিনিটের একটা শর্ট ফিল্ম, নাম – ওকে কাট।
এটা মূলত ছবি রিলিজের পরে দর্শক প্রতিক্রিয়া এবং ফারুকীর জবাবদিহিতা।
শুরুটা এরকম – ফারুকী বলছে কবে তার ছবি মুক্তি পেলো। কোন কোন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফ্যাস্টিভালে গেল। এরপরের দৃশ্যে মাঠ ভর্তি দর্শক চিৎকার করছে। হল থেকে দর্শক বের হচ্ছে, আনন্দ করছে, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের জয় ধ্বনিত হচ্ছে আকাশে বাতাসে।
এরপরের দৃশ্যগুলো দর্শক প্রতিক্রিয়া। ফেসবুকে ফারুকী ও সিনেমার বিরুদ্ধে অভিযোগ - ক্যাম্পেইন।
ফারুকীর বাবা (অভিনয়ে রুমি) ফারুকীকে বকা দিচ্ছে, কেন সে ইসলাম বিরোধী সিনেমা বানালো, কেন হিযবুয তাহরীর ফারুকীর বিরুদ্ধে মিছিল করছে, কেন ফারুকী তার বাবার শান্তি নষ্ট করছে...।
এরপরের দর্শকগুলো কোনো এক মহল্লার গলিতে থাকে।
শার্টের বোতাম খোলা একদল তরুণ বলে – ছবিটা অঅঅসাম হইসে।
আন্টি বয়েসী একজন বলে, সিনেমাটায় লিভ টু গেদার প্রমোট করছো ফারুকী, খুব খারাপ করছ। ফারুকীও ক্যামেরার পেছন থেকে জবাব দেয়।
এক তরুণী ফারুকীকে জানায় সিনেমার গল্প নাকি ঐ তরুণীর জীবন থেকে নেয়া হয়ে গেছে।
এরপরে আসে তিন প্রাক-যুবতী। ফারুকী ভাইয়্যা ভাইয়্যা করে মুখে ফেনা তুলে, অটোগ্রাফ চায়। ছবিটা অন্নেক ভাল্ল হয়েছে, অসাধারণ। এরকম ছবি চাই দাবী জানায়।
এক মধ্য বয়স্ক পুরুষ জানায় – "শুরুটা ভাল ছিল, ফিনিশিং ভাল হয় নাই। একটা মেয়ের সাথে দুইটা ছেলে, এটা কি হয় বলো?" ফারুকী জবাব দেয় – "ওরা তো বেড়াতে গেছে, একসাথে থাকতে যায় নাই।" কিন্তু, দর্শক মানে না... "একটা মেয়ের সাথে দুইটা স্বামী?"
পরের দর্শক এক ওভার ব্রীজের নিচে। ফারুকীর ছবি তোলে মোবাইল ফোনে।
ফারুকীর ক্যামেরা ব্রীজের ওপরে ওঠে, নামতে থাকা কিশোররা সিনেমাটির জন্য ফারুকীকে অভিবাদন জানায়।
এবার ব্রীজের ওপরে। স্যুট টাই পরা এক মধ্য বয়স্ক লোক এগিয়ে আসে (একে ফারুকী গ্রুপের নানা নাটকে নিয়মিত দেখা যায়)। লোকটি জিজ্ঞেস করে – ‘ভাই আপনি ফারুকী সাহেব না?... মুভিটির মাধ্যমে আপনি সমাজকে কী দিতে চেয়েছেন? এখানে আমি কনডম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, লীভ টুগেদার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, আপনি ছেক্স সমন্ধে খোলামেলা আলোচনা করেছেন...তরুণরা উচ্ছন্নে যাবে না?' ফারুকী পাল্টা যুক্তি দেয়, হিটলারের কথা বলে, পেছনে মানুষ জমে যায়। এগিয়ে আসে খোচা খোচা দাড়ির এক তরুণ, এসেই মধ্যবয়স্ক লোকটিকে ধমক দেয় ‘ভাই আপনি ফিল্ম সমন্ধে কিছু বোঝেন? ফিল্ম সম্পর্কে আইডিয়া আছে আপনার?’ লোকটি চুপ থাকে। এবার তরুণটি চিৎকার দেয় – ফারুকীকে বলে, “বস্, আপনি কোনো চিন্তা কইরেন না, সারা দেশের ইয়াং জেনারেশন আপনার পিছে আছে বস্, এই ধরনের সিনেমা আমরা সব সময় চাই বস্, সব সময়ের জন্য।‘ উল্লেখ্য তরুণটির গায়ে টি-শার্টে লেখা – Blowjob is better than no job.
এরপর আরো তরুণ তরুণী ফারুকীকে ধন্যবাদ দেয়, অটোগ্রাফ নেয়। এবার আসে ক্যাপ পরা এক তরুণ। একেও ফারুকী গ্রুপের নাটকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। সে জিজ্ঞেস করে – এই ছবি থেকে জাতি কী শিখবে? ফারুকী পালটা বলে, “আমি কি বলছি যে, আমি জাতির শিক্ষক?” তরুণটি জানায় এই ছবি দেখে ইয়াং জেনারেশন নষ্ট হয়ে যাবে। এবার ফারুকী জানায় সে নাকি একটা ছবি বানাবে এবার যেখানে সব ভাল থাকবে, ভাল ভাল লোক থাকবে, ভাল ভাল কথা বলবে; এর দুইমাস পরে বাংলাদেশের সব লোক যদি ভাল না হয়, সব দুর্নীতি যদি দূর না হয় ঐ তরুণের কী শাস্তি হবে? ফারুকীর এ যুক্তি শোনে তরুণটি সরে যায়।
এবারের দৃশ্যে ফারুকী তার ভাই-বেরাদারদের কাছে ফিরে আসে, এসে ঐ নেক্সট ছবির কনসেপ্টের কথা বলে, অ্যা নোবেল ফিল্ম, যেখানে সব কিছু ভাল ভাল থাকবে। যেহেতু সবাই ভাল হয়ে যাবে ছবির প্রথম সিকোয়েন্স হবে দুই পুলিস সব জামা কাপড় খুলে দিগম্বর হয়ে খোলা মাঠে চলে যাবে, যে দেশে অপরাধ নাই, সে দেশে উকিলেরও দরকার নাই, উকিল গাউনটাউন খুলে জমিতে চাষ করবে, এর পরে সবাই ঘরের তালা খুলে গার্বেজে ফেলে দেবে, সব বাড়ি ঘর দরজা জানালা খুলে ফেলে দেবে, কারণ দেশে সব ভাল হয়ে গেছে, প্রেমিক প্রেমিকারা বোরখা পরে দেখা করতে আসছে, আর লাস্ট শর্টে দেখা যাবে সূর্যাস্ত হচ্ছে, ডিরেক্টরের চেয়ার ফাঁকা, চেয়ারে আগুন লাগছে, কারণ যে দেশে সব কিছু সুখে শান্তিতে চলিতে লাগিল, যে দেশে কারো কোনো সমস্যা নাই, সে দেশে গল্প খুঁজে পাওয়া যাবে কোথায়? সব কিছু মাপা মাপা চলবে। ঐ দেশের ছবিতে ‘ওকে কাট’ বলে চলে যেতে হবে।
এই হলো ‘ওকে কাট’এর সংক্ষেপ। এ শর্ট ফিল্ম নাকি আবার রটারডামে কি একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয়েছে!
ছবি বানানোর পরে এমন জবাবদিহিতার কোনো দরকার আছে কিনা সেটা বিরাট প্রশ্ন। এতসব স্বতঃপ্রণোদিত কারণ দর্শানোকে বরং ছবির পাবলিসিটি বলে মনে হয়েছে।
থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সিনেমা দেখে যদি সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, ‘অ্যা নোবেল ফিল্ম’ দেখে দেশের সব মানুষ ভালো হবে কিনা – ফারুকীর এমন যুক্তিকে খোঁড়া মনে হয়েছে। রাতে ড্রাম বাজিয়ে মহল্লার মানুষের ঘুম নষ্ট করার অভিযোগ করলে ড্রামার যদি পালটা যুক্তি দেয় – কাল থেকে আমি ড্রামের বদলে বাঁশী বাজাবো, দেখি সবাই শান্তিতে ঘুমায় কিনা – সবাই না ঘুমালে বলেন- আপনার কী শাস্তি হবে? এরকমই অসামঞ্জস্য মনে হয়েছে ফারুকীর যুক্তিকে।
স্পেশাল ফিচারের এইসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আত্মপক্ষ সমর্থন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের দূর্বলতাকেই প্রমাণ করে।


 আরিফ জেবতিক
আরিফ জেবতিক